তড়িতের সাথে চুম্বকের সম্পর্কের কথা মনে আছে বন্ধুরা? এবার শুনলে অবাক হবে যে চুম্বকফ্লাক্স নামে একটা ব্যাপার আছে যেটা আসলে চৌম্বক পদার্থের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের মত করেই চলাচল করে। ফেরোচুম্বক পদার্থ এই ফ্লাক্সের চলাচলের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। সহজ কথায় বললে এরা হলো চুম্বক সুপরিবাহী।

চিত্র-২.১ এবং চিত্র-২.২ এর দিকে তাকাও এবং তোমাদের পূর্বপরিচিত বিদ্যুৎ বর্তনীর সাথে পাশের চিত্র-২.১ চিত্রখানার কোন মিল খুঁজে পাও কি? বিদ্যুৎ বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ বর্তনীর একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে পরিবাহীর মাধ্যমে চলাচল করে। একইভাবে ২য় বর্তনীতে (চিত্র-২.২) চুম্বক ফ্লাক্স প্রবাহিত হচ্ছে। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় বিদ্যুৎ বর্তনির উৎসের তড়িচ্চালক বলের জন্য আর চুম্বকের বর্তনীর ক্ষেত্রে চুম্বক ফ্লাক্সের সৃষ্টি হয় চুম্বকচ্চালক (Magnetomotive Force) বলের জন্য।

চুম্বকচ্চালক বলের সৃষ্টি হয় চিত্রের (চিত্র-২.২) প্যাঁচানো কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহের ফলে উৎপন্ন চুম্বকক্রিয়া থেকে। বৈদ্যুতিক বর্তনীতে যেমন রোধ তড়িৎ প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে তেমনি চুম্বকফ্লাক্সকেও রিলাকটেন্স (Reluctance) এর বাধায় পড়তে হয়। এমন কিছু পদার্থ আছে যারা কখনই বা কোন অবস্থাতেই চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না এবং কোন উপায়েই তাদেরকে চুম্বকে পরিণত করা যায় না। এসব পদার্থকে বলা হয় ডায়াচুম্বক।
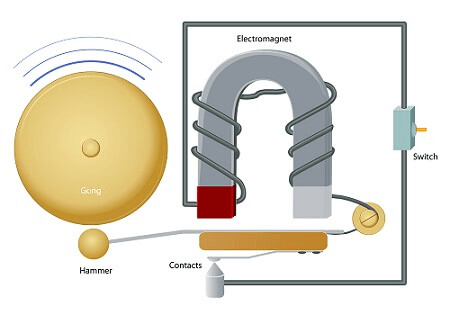
সহজ কথায় বললে এদের মধ্যকার অণু চুম্বক পদার্থগুলো কখনই সম্মিলিতভাবে চুম্বক তৈরি করতে পারে না (পানি আমাদের সবচেয়ে পরিচিত ডায়াচুম্বক পদার্থ)। ফলশ্রুতিতে ডায়াচুম্বক পদার্থ চুম্বককে তো কাছে টানেই না উল্টো দূরে ঠেলে দেয় অর্থাৎ বিকর্ষণ করে। তো এদের আপেক্ষিক প্রবেশ্যতার অবস্থাটা কী? কী আর হবে? ১ এর চেয়ে কম। মানে চুম্বকের বলরেখার জন্য এসব পদার্থের চেয়ে শূন্য মাধ্যম আরামদায়ক। এই দুই পদার্থের মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্য সম্বলিত পদার্থগুলোকে প্যারাচুম্বক পদার্থ নামে ডাকা হয়। চুম্বকের দিকে এসব পদার্থ মাঝারিভাবে আকৃষ্ট হয়। আমাদের বেঁচে থাকার অতি প্রয়োজনীয় অক্সিজেন (O2) এই দলের পদার্থ। অন্য চুম্বকের বলরেখা এই পদার্থগুলো দিয়ে শূন্যমাধ্যমের চেয়ে সহজে গমন করতে পারে কিন্তু ফেরোচুম্বকের মত নয়। তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে, আপেক্ষিক প্রবেশ্যতার মান ১ এর চেয়ে হয়ত বেশি কিন্তু খুব বেশি নয়।
ধরো, তুমি দুইটা বিশাল মোটা মোটা দণ্ডাকার চুম্বক নিয়ে এতদিনের পড়ার উপর ভিত্তি করে কিছু আবিষ্কারের নেশায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে বসে গেছো। হিসেব করে দেখলে তোমার দণ্ডগুলো আসলে ২ (মিটার) প্রস্থচ্ছেদের। একটার উত্তর মেরু আরেকটার দক্ষিণ মেরুর কাছে রাখলে । তো এখন বলরেখাগুলো উত্তর মেরু থেকে বের হয়ে খুবই তাড়াতাড়ি তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষিণমেরু পেয়ে যাবে এবং সে খুশিতে সোজাসুজি প্রবেশ করবে। ধরো, মোট ১০০টি বলরেখা এই ২ (মিটার) উত্তর মেরু থেকে বের হয়ে আবার ২ (মিটার) ২ দক্ষিণ মেরুতে প্রবেশ করলো। তাহলে বলো দেখি ১ মিটার থেকে কয়টা আসবে ? একদম ঠিক ধরেছো, ৫০টি। এই ৫০ টিকে বলা হয় ফ্লাক্স। আবার, চৌম্বকবলরেখা লম্বভাবে বের হয়। তাই না ? এভাবে একইভাবে চৌম্বক বলরেখার চলার পথে যদি তুমি লম্বভাবে একটা ১ (মিটার)` বা সাধারণ কথায় একক ক্ষেত্রফল এর জায়গা জুড়ে ঠিক কয়টা বলরেখা গেলো এটার হিসাব করে ফেলতে পারো তাহলে আসলে তুমি ঐ জায়গার চৌম্বকফ্লাক্স বের করে ফেলবে। গাণিতিকভাবে এটার হিসাব করা হয়, চৌম্বকক্ষেত্র আর অতিক্রান্ত ক্ষেত্রফলের মধ্যে ভেক্টরের স্কেলার গুণন করে। = BAcosa
(চলবে...)